Citizen Journalism
নাগরিক সাংবাদিকতা / Citizen Journalism
v স্বতস্ফূর্ত ও স্বপ্রণোদিত হয়ে গণমানুষের খবর ও তথ্য সংগ্রহ, পরিবেশন, বিশ্লেষণ এবং প্রচারে অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে সিটিজেন জার্নালিজম বা নাগরিক সাংবাদিকতা। এ সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি, পরিচয় এবং প্রশিক্ষণ ছাড়াই আধুনিক প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে সাধারণ জনগণ নিজেরা বা অন্যের সহায়তায় তথ্যের আদান প্রদান করে থাকে। নাগরিক সাংবাদিকতার ধারণায় মূল ধারার গণমাধ্যমে যারা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে বিবেচিত হন তারাই মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরস্পরের তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে থাকেন।
সিটিজেন জার্নালিজমের মাধ্যমে একজন সচেতন নাগরিক তার নিজের জ্ঞান ও সৃজনশীলতা সমাজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করতে পারেন। আর তাই, সাংবাদিকতার কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা পরিচয় ছাড়া অনলাইন ভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যখন কেউ তার চারপাশের ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা, বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মতামত কিংবা সঠিক তথ্য-উপাত্ত লেখনী, তথ্যচিত্র, ইনফোগ্রাফিক্স, ক্ষুদেবার্তা, অডিও, ভিডিও বা অন্য কোনো ভাবে জনস্বার্থে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে প্রচার বা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে নাগরিক সাংবাদিকতা বলা যেতে পারে।
এর আরও অনেক নাম অাছে –
- স্ট্রিট জার্নালিজম (Street Journalism)
- পাবলিক জার্নালিজম (Public Journalism)
- ডেমোক্রেটিক জার্নালিজম (Democratic Journalism)
- পারটিসিপেটরি জার্নালিজম (Participatory Journalism)
- প্রান্তীক জার্নালিজম (Grassroots Journalism)
- নেটওয়ার্ক জার্নালিজম (Network Journalism)
- ওপেন সোর্স জার্নালিজম (Open Source Journalism)
- হাইপার লোকাল জার্নালিজম (Hyper local Journalism)
- বটম-আপ জার্নালিজম (Bottom-up Journalism)
- স্ট্যান্ড অ্যালন জার্নালিজম (Stand alone Journalism)
- ডিস্ট্রিবিউটেড জার্নালিজম (Distributed Journalism)
নাগরিক সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশ:
নব্বই’র দশকে ইন্টারনেট ভিত্তিক world wide web এর আর্বিভাবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উদ্ভব। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি’র ছাত্র ক্রিস অ্যান্ডারন্স বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সিয়াটলে গৃহীত বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৯৯ সালে ‘ইন্ডিমিডিয়া’ (Indy media) নামে নাগরিক সাংবাদিকতার (সিটিজেন জার্নালিজম) প্রথম স্বীকৃত প্লাটফরম প্রতিষ্ঠা করেন।
বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন গুগলের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৮ সালে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক ২০০৪ সালে, টুইটার ২০০৬ সালে এবং অ্যাপলে-আই ফোন ২০০৭ সালে। এদের আর্বিভাব ও উদ্ভাবন নাগরিক সাংবাদিকতার ধারণা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একইসাথে সহজ প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্টফোনের আর্বিভাব নাগরিক সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করছে।
·
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ, ছবি, ভিডিও ধারণ ও আপলোড করার সুবিধা নাগরিক সাংবাদিকতা আরও সহজতর করেছে।
·
তবে স্বীকৃত না হলেও নাগরিক সাংবাদিকতার ধারণা একেবারেই নতুন কিছু নয়। আব্রাহাম জ্যাপ্রুডার জন এফ কেনেডি’র হত্যাকান্ডের ভিডিওচিত্রটি ধারণ করেছিলেন একটি সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে। অনেকেই তাকে নাগরিক সাংবাদিকতার জনক বলে মনে করেন।
·
এখন সিএনএন, বিবিসি, আল জাজিরা, ও বিডিনিউজের মতো মূল ধারার গণমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিক সাংবাদিকতার ওপর নির্ভর করছে। সংবাদ সূত্র হিসেবে নাগরিক সাংবাদিকদের ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিটি প্রতিবেদনের শেষাংশে ঘটনাস্থলের আশেপাশের পাঠকদের তাঁদের মতামত বা মন্তব্য তুলে ধরতে অনুরোধ করছে। আর সাম্প্রতিক এই ধারা থেকে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে মূল ধারার গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত অনেক সংবাদই প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।
প্রত্যেকেরই সাংবাদিক হিসেবে ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। প্রকাশিত অডিও, ভিডিও ও প্রতিবেদন সম্পর্কে আগ্রহী যে কারো মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে। যে কেউ মন্তব্য, বিতর্ক বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রবল থাকে বিবেকপ্রষূত শুভবুদ্ধি নাগরিক সাংবাদিকতার নৈতিকতার একমাত্র মাপকাঠি।
নাগরিক সাংবাদিকতার তিন মডেল
1)
Slashdot-Ohmynews মডেলের নাগরিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যবহারিকারিদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
2)
Indymedia মডেলের নাগরিক সাংবাদিকতায় যে কেউ মন্তব্য এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠকের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়, সে কোনটা গ্রহণ বা বর্জন করবে।
3)
Wiki based মডেলের নাগরিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপলোড করা যে কোনো প্রতিবেদন চাইলে যে কেউ সম্পাদনা বা তথ্য-উপাত্ত যোগ করতে পারে, এতে করে কোনো একটা প্রতিবেদন বিশেষ কোনো ব্যক্তির একার নয়, বরং অনেকের অবদান থাকে তাতে।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনের কিছু উদাহরণ
·
২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভয়বহ সন্ত্রাসী হামলার ভিডিও চিত্র ধারণ করেছিলেন যারা তারা কেউই কিন্তু পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন না।
·
২০০৪ সালে সুনামির আঘাতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার লক্ষ্যে ক্ষয়ক্ষতির গুরুত্ব বিবেচনায় ত্রাণ তৎপরতা পরিচালায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
·
২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনের ভয়াবহ বোমা হামলার ঘটনাটি একজন সাধারণ নাগরিক মোবাইল ফোনে ধারণ করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে বিবিসি, সিএনএন ও এমএসএনবিসিসহ অন্যান্য মূল ধারার গণমাধ্যমসমূহ প্রচার করেছে।
·
২০০৫ সালে আমেরিকার হ্যারিকেন ক্যাটরিনা ও রিতা আঘাত হানলে সাধারণ জনগণই স্বপ্রনোদিতভাবে স্থানীয় খবরাখবর সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছিলো।
·
পাকিস্তানের আবোটাবাদে বিন লাদেনের গোপন আস্তানায় মার্কিন বিশেষ বাহিনীর সিক্রেট মিশন চলাকালীন সময়ে ঘটনাস্থলের ২ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্য থেকে সোয়াইব আতাহার নামে একজন নাগরিক সাংবাদিক লাইভ টুইট করেছিলেন। যা সত্যিকার অর্থে ঐদিন কী ঘটেছিল তার সঠিক বিবরণ বলে মনে করা হয়।
·
২০০৬ সালে বিষাক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আইসল্যান্ডের ব্যাঙ্কিং খাতের অব্যবস্থাপনার নানা দিক নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে উইকিলিকস এর জন্ম। কিন্তু ২০১০ সালে বাগদাদে মার্কিন বিমান হামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক ইরাকিসহ রয়টার্সের দু’জন সাংবাদিক নিহত। মূল ধারার অনেক গণমাধ্যমই প্রকৃত সত্য ঘটনাকে এড়িয়ে যায় এবং উইকিলিকস
Collateral Murder শিরোনামের ভিডিও ফুটেজ প্রচারের মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসে। পরবর্তী সময়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার দু’লাখ পঞ্চাশ হাজার গোপন নথি ফাঁস করে দিয়েছে। সম্প্রতি পানামা পেপারস নামে পরিচিত মোজেস ফনসেকার মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত গোপন নথি প্রকাশ হওয়াতে। অনেক দেশের সরকার প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়েছে।
·
২০১০ সালের আরব বসন্ত এবং ২০১১ সালের লন্ডনের দাঙ্গার ঘটনায় নাগরিক সাংবাদিকতার প্রতি মানুষের আস্থা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
বাংলাদেশে নাগরিক সাংবাদিকতা
· বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ‘সামহোয়ারইনব্লগ’ বাঁধ ভাঙার আওয়াজ শিরোনামে বাংলাদেশে নাগরিক সাংবাদিকতার সূচনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘মুক্তমনা’সহ আরো অনেক জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত ব্লগ এর আর্বিভাব হয়েছে। এছাড়া মূল ধারার গণমাধ্যম ‘বিডিনিউজ’ ও আরপি নিউজসহ অনেকেই এখন পাঠকের মতামতকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরার লক্ষ্যে সিটিজেন জার্নালিজম কর্নার চালু করেছে। পাশাপাশি ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেজবুক তরুণ প্রজন্মের পছন্দের শীর্ষে অবস্থান করায় নাগরিক সাংবাদিকতা বিস্তারের অবারিত সুযোগ রয়েছে।
নাগরিক সাংবাদিকতার কিছু দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়েছে- বিডিয়ার বিদ্রোহের ঘটনা, গণজাগরণ মঞ্চ, ভিকারুনন্নেসা নুন স্কুলের ছাত্রী নির্যাতন।
নাগরিক সাংবাদিকতার ইতিবাচক দিক:
·
সম্পূর্ণ বিকল্প একটি মাধ্যম, যা বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সাহায্য করবে। প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট যে কোনো দৃর্যোগ-দুর্বিপাকে প্রত্যক্ষদর্শীর মতামত ও বর্ণনা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। এলিট বা সমাজের প্রভাবশালীদের প্রভাব থেকে মুক্ত। সমাজের প্রান্তীক জনগোষ্ঠীর মূখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ। মূলধারার গণমাধ্যমে অপ্রকাশিত বা গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত বিষয় এখানে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানি ও সরকারের প্রভাবমুক্ত। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ। নির্দিষ্ট কোনো ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আটকে না থেকে একজন বিশ্ব নাগরিক হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় অংশগ্রহণমূলক সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিকাশ। সার্বজনীন কল্যাণে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে।
নাগরিক সাংবাদিকতার নেতিবাচক দিকসমূহ:
·
ধর্মান্ধ, উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রচলিত মূলধারার গণমাধ্যমের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতে পারে। বিষয়াশ্রিত এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রকট হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাগরিক সাংবাদিকতা ‘সফট নিউজ’ বা ফিচারধর্মী লেখা প্রচারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।
নাগরিক সাংবাদিকতায় নীতি নৈতিকতা:
· মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কোনো তথ্য-উপাত্তের প্রচার ও প্রকাশ থেকে বিরত থাকা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জন-গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং ব্যক্তির মর্যাদাহানীকর কোনো বিষয়ের প্রকাশ ও প্রচার থেকে বিরত থাকা। নিজের বিবেকের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা।
Thank You






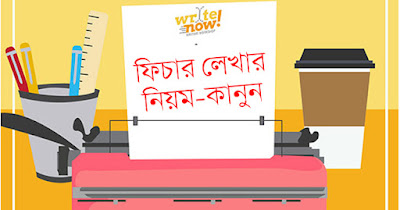
মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন